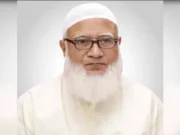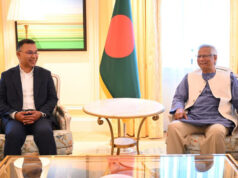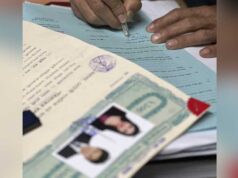আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশ এমনই একজন কবি, যিনি জীবন, সময়, প্রকৃতি ও মৃত্যুকে এক রহস্যময় নন্দনতত্ত্বে মিশিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পর তিনি বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছেন নতুন ভাষা, ভঙ্গি ও চিন্তার ধারা-যেখানে মৃত্যু কোনো আতঙ্ক নয়; বরং জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি; এক গভীর, দার্শনিক ও আত্মমুক্তির প্রকাশ। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মৃত্যুবোধ এসেছে নিঃসঙ্গতার গভীর গহ্বর থেকে। তার কবিতায় মৃত্যু মানে শুধু সমাপ্তি নয়, বরং আত্মার এক রূপান্তর-এক অনন্তের দিকে যাত্রা, যেখানে সময় ও ক্লান্তির অবসান ঘটে।
জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) ছিলেন এমন এক সময়ের কবি, যখন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংকট ও সামাজিক অস্থিরতা মানুষকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। নিজেও তিনি ছিলেন গভীরভাবে আত্মমগ্ন, অন্তর্মুখী ও নিঃসঙ্গ স্বভাবের। তিনি কলকাতার শহুরে বিশৃঙ্খলায় বসবাস করেও নিজের মনের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় ও স্মৃতির অরণ্যে। তার এই নিঃসঙ্গতার ভেতর থেকেই জন্ম নেয় এক গভীর মৃত্যুচেতনা-যা ভয় বা আতঙ্কের নয়, বরং অন্তর্গত প্রশান্তিজারিত।
‘বনলতা সেন’ কবিতায় তিনি বলেন-‘এই পৃথিবীর ক্লান্ত পথিক আমি,/ দুই পায়ের চিহ্ন রেখে গেছি সাত সমুদ্র তের নদীর তীরে।’ পঙ্ক্তিগুলোয় স্পষ্ট যে, মৃত্যু তার কাছে যাত্রার শেষ নয়-বরং এক দীর্ঘ যাত্রার নির্মল বিশ্রাম।
জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মৃত্যুকে কখনোই ধ্বংস বা অনন্ত অন্ধকার হিসেবে দেখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করতেন, মৃত্যু হলো জীবনের পরিণতি, যা মানুষকে প্রকৃতির চিরচক্রে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এ জন্য তার কাব্যচেতনায় মৃত্যু মানে অবসান নয়, বরং পুনর্জন্ম বা রূপান্তর।
‘অবশেষে’ কবিতায় তিনি লিখেছেন-‘অবশেষে সবকিছু মুছে যাবে,/শুধু রবে নক্ষত্র, ধানক্ষেত আর নীরব নদী।’ এই পঙক্তিতে মৃত্যু এক চিরস্থায়ী প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের প্রতীক হিসেবে উপলব্ধি করা যায়। কেননা, মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হলেও তা প্রকৃতির অবিনশ্বর রূপে ফিরে আসে। অতএব, মৃত্যু এখানে জীবনের পরিণত ধারাবাহিকতা, কোনো শূন্যতা নয়।
লেখাই বাহুল্য, প্রকৃতি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার কাছে প্রকৃতি শুধু দৃশ্য নয়, বরং জীবনের প্রতিরূপ, যেখানে জন্ম-বৃদ্ধি-ক্ষয় ও মৃত্যু এক অবিচ্ছিন্ন চক্রে যুক্ত। তার কবিতায় শরতের পাতা ঝরা, নদীর নিস্তব্ধ ধারা, কিংবা রাতের অন্ধকার-সবকিছুই মৃত্যু ও সময়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
‘আমি হেমন্তের কথা বলছি’ কবিতায় তিনি লিখেছেন-‘আমি হেমন্তের কথা বলছি, যেখানে ফসলের পর মাঠ ফাঁকা হয়ে যায়,/ আর আকাশে থাকে এক নিঃসঙ্গ তারা।’ এখানে হেমন্ত কেবল একটি ঋতু নয়; এটি জীবনের শেষ অধ্যায়, যেখানে মৃত্যু এক নিঃশব্দ, স্বাভাবিক রূপে উপস্থিত থাকে। জীবনানন্দের এই প্রকৃতিচেতনা মৃত্যু-ভাবনাকেও করে তোলে নন্দনীয় ও দার্শনিক।
বিশ্লেষকদের মতে, জীবনানন্দ ছিলেন এক অস্তিত্ববাদী কবি। তার কবিতায় মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন, সময়ের নিঃশব্দ প্রবাহ, আর মৃত্যুর অপরিহার্যতা রয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিঃশেষ হয়, কিন্তু প্রকৃতি ও সৃষ্টি চিরন্তন। আর এই উপলব্ধিই জীবনানন্দের মৃত্যুবোধকে করেছে গভীর।
‘ঘর’ কবিতায় তিনি লিখেছেন-‘আমি যে ঘরে থাকি, সে ঘর সময়ের মধ্যে ডুবে যায়,/ তবুও আমি থাকি নদীর ধারে এক শালিকের মতো।’ এই পঙক্তিতে মৃত্যু মানে সময়ের গহ্বরে ডুবে যাওয়া, কিন্তু প্রকৃতির মাধ্যমে আবারও চিরন্তনে ফিরে আসা। তার দৃষ্টিতে মৃত্যু হলো মানুষের আত্মার অনন্তে গমন, যেখানে কোনো ভয় নেই, আছে শুধু শান্তি ও নির্লিপ্ততা।
জীবনানন্দের জীবনে একাকীত্ব ছিল স্থায়ী সঙ্গী। কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা, সামাজিক অবমূল্যায়ন এবং পারিবারিক চাপ তার ভেতরে তৈরি করেছিল গভীর বিষণ্নতা। তবু তিনি মৃত্যুকে অন্ধকার হিসেবে দেখেননি। বরং মৃত্যুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন অন্তরের প্রশান্তি ও মুক্তির আলোকিত পথ।
তার শেষ জীবনে লেখা কবিতাগুলোতে মৃত্যু যেন আরও নিবিড় হয়ে ধরা দেয়। কবিতায় দেখা যায়, মৃত্যুর সঙ্গে এক গভীর মৈত্রী গড়ে উঠেছে। ‘অন্ধকার’ কবিতায় তিনি বলেন-‘আমি অন্ধকারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম,/ দেখলাম, ওর ভেতরে আলো আছে।’ এখানে মৃত্যু এক রহস্যময় আলো, যা জীবনের ক্লান্তি দূর করে। এই অনুভূতিই জীবনানন্দকে করে তোলে মৃত্যুর কবি, কিন্তু নৈরাশ্যের নয়-বরং আলো ও শান্তির কবি।
জীবনানন্দ দাশ সময়কে অনুভব করেছিলেন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ হিসেবে। তার কাছে মৃত্যু হলো সেই সময়েরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে ব্যক্তি হারিয়ে যায়, কিন্তু সময় থাকে চিরন্তন। তিনি লিখেছেন-‘সময় নদীর মতো বয়ে যায়,/ মানুষ তার কূল ধরে হাঁটে, ফিরে আসে না।’ এখানে মৃত্যু সময়ের প্রবাহে আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে ধরা দেয়।
জীবনানন্দ জানতেন, সময়ের বিরুদ্ধে মানুষ লড়তে পারে না। তাই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন এক স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে, কোনো পরাজয় হিসেবে নয়। আর মৃত্যুভাবনা তাকে পরিণত করেছে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্তর্মুখী প্রতিভা হিসেবে; যিনি মৃত্যুকে ভয় নয়, শিল্পে রূপ দিয়েছেন।
সূত্র:যায়যায় দিন